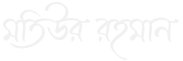পূর্ণেন্দু পত্রী: গোটা বাংলার মানুষ বলেই
পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে কলকাতায় প্রথম দেখা হয়েছিল ‘প্রতিক্ষণ’ অফিসে, সেটা ১৯৮৭ সালের জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের কোনো এক দিন। মনে পড়ে, তাঁর সল্টলেকের বাসায় আমার দীর্ঘ সময় কেটেছে বই, নাটক, সিনেমা আর লেখালেখি নিয়ে কথা বলে, আলোচনা করে। ১৯৮৯ সালে তিনি একবার ঢাকায় এসেছিলেন, সে সময়ের স্মৃতিগুলো এখনো বড় বেশি করে বাজে। সেসব কথা এখন পুরো মনে না থাকলেও তার রেশ আজও বহমান, সজীব।
একবার কলকাতায় পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে একটা নাটক দেখতে গিয়েছিলাম (২০ আগস্ট ১৯৮৭)। নাটকের নামটি এখন আর মনে নেই, অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী চক্রবর্তীসহ অনেকে। অভিনয় শেষে আমরা প্রথমে যাই সৌমিত্রের কাছে। তারপর পূর্ণেন্দু পত্রী ‘মাধবী, মাধবী’ বলে ডেকে তাঁর সাজঘরে গিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্যারিস থেকে আনা দুটি পারফিউম দিলেন তাঁকে। বললেন, ‘প্যারিস থেকে তোমার জন্য এনেছিলাম।’ মাধবী সে উপহার নিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর শারীরিক কুশলতা জানতে চাইলেন। সেদিন মাধবী চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলার পর অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আবার দেখা করেছিলাম। দুজনই খুশি হয়ে অটোগ্রাফ দিয়েছিলেন। তারপর যতবার পূর্ণেন্দু পত্রীর কথা মনে হয়, সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়ে, সেই কণ্ঠে ‘মাধবী, মাধবী’ ডাক যেন শুনতে পাই।
শুনেছিলাম, ‘স্ত্রীর পত্র’-এর নায়িকা মাধবী চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা পূর্ণেন্দু পত্রী লালন করেছিলেন বহুদিন; হয়তো মৃত্যু পর্যন্ত, কে জানে! এভাবে কাছ থেকে দেখা, দূর থেকে জানা পূর্ণেন্দু পত্রীকে নিয়ে স্মৃতির শেষ নেই।
মনে পড়ে, পঞ্চাশের দশকের মধ্যভাগে নতুন সাহিত্য পত্রিকার কোনো শারদীয় সংখ্যায় ‘ডাবল ডেকার’ লেখাটির নিচে প্রথম দেখেছিলাম পূর্ণেন্দুশেখর পত্রীর নাম। যদিও তার আগেই ১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘এক মুঠো রোদ’। তারপর সমুদ্র গুপ্ত নামে শহর ‘কলকাতার আদিপর্ব’ লিখলেও আমরা সে কথা জানতাম না। কিন্তু ষাটের দশকের শুরু থেকে আমরা তাঁকে একজন আধুনিক প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে জেনেছি বেশি।
ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রথম উপন্যাস ‘দাঁড়ের ময়না’ (১৯৫৮) পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। তখন আমরা বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাবে দারুণ মানিক-ভক্ত। দাঁড়ের ময়নাতে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়া পেয়েছিলাম। তারও পরে আরও জানতে পারি, কবিতা, প্রবন্ধ আর উপন্যাসের পর পূর্ণেন্দু পত্রী সিনেমাজগতে ঢুকেছেন। সেটা ছিল আমাদের জন্য তখন এক বড় খবর। শুধু তা-ই নয়, দ্বিতীয় ছবিতেই জাতীয় পুরস্কার এবং তারপর যত জেনেছি, ততই অবাক হয়েছি আর ভেবেছি, একজন মানুষ কত দিতে পারে?
সাহিত্য-সংস্কৃতির একাধিক বা বহু শাখা-প্রশাখায় যাঁদের দীপ্ত ও সফল পদচারণ, তাঁদের সম্পর্কে আগ্রহ আমার প্রবল। তবে এ প্রশ্নও মনে জাগে, একজন লেখক বা শিল্পীর বহুমাত্রিক সৃষ্টিশীল সক্রিয়তা সুফল বয়ে আনতে পারে কতটা? এতে কি সৃজনশীলতার কোনো একটা বিশেষ ক্ষেত্রে বিশাল সফলতার সুপ্ত সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে যায় না?
এ ধরনের বহু প্রশ্ন নিয়ে ১৯৮৭ সালের জুন মাসের এক সকালে, শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে, সল্টলেক সিটিতে পূর্ণেন্দু পত্রীর বাসভবনে গিয়ে হাজির হই। তাঁর বাসায় যাওয়ার দিনক্ষণ অবশ্য আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমি যথাসময়ে পৌঁছাতে পারিনি। দেরি হওয়াতে তিনি কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কলকাতায় আমি নতুন। রাস্তাঘাট তেমন চিনি না। তাঁর উত্কণ্ঠা সেখানেই। অবশ্য নির্দিষ্ট বাসস্টপে নেমে তাঁর বাসা চিনে নিতে কোনো কষ্ট হয়নি আমার। সিনেমা করেন যে পূর্ণেন্দু পত্রী, তাঁর বাসা চিনিয়ে দেওয়ার মতো লোকের অভাব হয়নি রৌদ্রোজ্জ্বল সেই সকালে।
পূর্ণেন্দু পত্রী সম্পর্কে বহুদিনের আগ্রহ এবং নানা প্রশ্নের জবাব পেতে গিয়ে দেখি তাঁর সম্পর্কে খুব অল্পই জানি। বিগত কয়েক দশকের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির বহুমুখী প্রবাহের সঙ্গে যাঁদের কিছুটা হলেও পরিচয় বা যোগাযোগ রয়েছে, তাঁদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া কঠিন হবে, যিনি পূর্ণেন্দু পত্রীর নাম জানেন না বা শোনেননি। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ, উভয় অঞ্চলের জন্যই এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।
সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে লেখক পূর্ণেন্দু পত্রীর বিচরণ ছিল না। তাঁর মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা ষাটের অধিক। ১৯৫১ থেকে ’৮৭-এর জুন পর্যন্ত তাঁর দশটির অধিক কবিতার বই প্রকাশিত হয়। এমনকি পৌনে দুশ পৃষ্ঠার পূর্ণেন্দু পত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতার দ্বিতীয় সংস্করণও বের হয়ে গিয়েছিল ১৯৮৭ সালেই।
পূর্ণেন্দু পত্রীর উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে পাঁচটি। প্রথম উপন্যাস ‘দাঁড়ের ময়না’ মানিক স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছিল। তবে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস ‘মহারাণী’-ই তাঁর সেরা রচনা বলে তিনি মনে করেন। উপন্যাসে নায়িকা পার্বতীর বয়স পঁচানব্বই বছর। আরও প্রায় পাঁচটি উপন্যাস ছাপার অপেক্ষায় ছিল তখন।
প্রবন্ধ-সাহিত্যের বইয়ের সংখ্যা তখন ছিল ১০। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো ‘রূপসী বাংলার দুই কবি’, যা মনীষী-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর কবি জীবনানন্দ দাশের কাজের তুলনামূলক আলোচনা। বিরল দৃষ্টান্তহীন এ ধরনের একটা বই হয়তো পূর্ণেন্দু পত্রীর মতো একজন উঁচু মানের শিল্পী ও কবির পক্ষেই লেখা সম্ভব। তখন বের হয়েছে ‘মোনালিসা’, ‘রবীন্দ্রনাথ না-রবীন্দ্রনাথ’, ‘সাহিত্যে তাজমহল’, ‘গোলাপ যে নামে ডাকো’, ‘হ্যাঁ কলকাতা কলকাতা’, ‘রোদ্যাঁ’ প্রভৃতি বই বা সম্পাদিত আকর্ষণীয় মিনি বইগুলো, যেগুলো থেকে আমরা অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানতে পারি। প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত ‘কবিতার ঘর ও বাহির’, ‘কালি কলম মন’, ‘সিনেমা সিনেমা’, ‘শিল্প সংক্রান্ত’, ‘সাহিত্য সংক্রান্ত’ বা ‘সিনেমা সংক্রান্ত’ প্রভৃতি অত্যন্ত সুখপাঠ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ বই, যা থেকে আমরা সহজেই পেয়ে যাই বিশ্বসংস্কৃতির ভান্ডার থেকে তুলে আনা হৃদয়স্পর্শী অজানা সব তথ্য। অন্যের কথা জানি না, কিন্তু এসব বই আমার মতো বহু পাঠককে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করবে, বহু অজানাকে জানার আনন্দে উদ্বেল করে তুলবে।
ইতিহাসবিদ হিসেবে পূর্ণেন্দু পত্রীর পরিচয় আমাদের তেমন জানা নেই। কলকাতার অতীত নিয়ে তিনি ছোট-বড় বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর সমুদ্র গুপ্ত ছদ্মনামে প্রকাশিত ‘শহর কলকাতার আদিপর্ব’-এর জন্য তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। সে-ও অনেক দিনের কথা। তবে কলকাতা নিয়ে ছোটদের জন্যও বই লিখেছিলেন। আরও বিস্ময়কর হলো,‘ বঙ্গভঙ্গ’ নামে তাঁর প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বইটির প্রথম সংস্করণ বহু আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। পত্রীর ইচ্ছে ছিল এটিকে আরও বর্ধিত আকারে নতুন করে বের করবেন। সেটা শেষ পর্যন্ত করতে পেরেছিলেন কি না, জানি না।
ষাটের দশকের শেষ ভাগে, পূর্ণেন্দু পত্রী ঝড়ের বেগে সিনেমাজগতে প্রবেশ করে রীতিমতো তোলপাড় ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা ‘স্বপ্ন নিয়ে’ প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ অবলম্বনে তৈরি করেছিলেন। তার পরই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প থেকে ‘স্ত্রীর পত্র’ করেন ১৯৭২ সালে। ছবিটি পত্রীর জন্য বিশেষ সম্মান নিয়ে আসে। এটি সে বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা সিনেমা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়ে যায়। পূর্ণেন্দু পত্রী পুরস্কৃত হন। এরপর ‘ছেঁড়া তমসুক’ (সমরেশ বসু), ‘মালঞ্চ’ (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’ (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)—এই ছবি তিনটি করেন। সুচিত্রা সেনকে নায়িকা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের শুটিং এক দিন হওয়ার পর ছবিটির প্রযোজকের আত্মহত্যার কারণে তা আর এগোয়নি। তিনি বলেছিলেন, সুচিত্রা সেন খুবই উত্সাহী ছিলেন ছবিটির ব্যাপারে।
পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ছাড়াও পূর্ণেন্দু পত্রী চারটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ডকুমেন্টারি করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে বাংলার পট ও কালীঘাটের পট এবং শিল্প-ভাস্কর্যে গীত-গোবিন্দের প্রভাব নিয়ে এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের ডকুমেন্টারিগুলো করেন। এরপর তিনি ছবি করার আর বিশেষ কোনো উত্সাহ পাননি।
একসময় তো আমাদের কাছে পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রধান পরিচয় ছিল একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, মূলত প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবেই। অথচ মজার কথা হলো, পত্রী কলকাতা আর্ট কলেজে তিন বছর পড়ার পর ধর্মঘটের কারণে কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে আর ফিরে যাননি ধরাবাঁধা শিক্ষা বা শিল্পচর্চার শিক্ষাকেন্দ্রে। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে পূর্ণেন্দু পত্রী প্রচ্ছদশিল্পী হিসেবে রাজকীয় আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই শাখাতে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলা পুস্তক প্রকাশনার জগতে সৌকর্যের সুউচ্চ যে মান পত্রী সৃষ্টি করে গেছেন, তা অবাক করার মতো। তাঁর আঁকা প্রচ্ছদের সংখ্যা কত শত বা হাজার, তার হিসাব কেউ জানেন না। তিনিও হিসাব বলতে পারেননি।
শেষ এক দশকেরও বেশি সময় পূর্ণেন্দু পত্রী লেখালেখিতেই মনোযোগী ছিলেন বেশি। তার পরও তিনি কলকাতার সুন্দর রুচিশীল প্রতিক্ষণ পত্রিকা ও প্রকাশনার শিল্পনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন। তারপর দৈনিক ‘আজকাল’-এর সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন।
এসব বহুধাবিস্তৃত বিভিন্নমুখী কাজের পাশাপাশি বিস্ময়কর হলেও সত্য যে পূর্ণেন্দু পত্রী সৃজনশীল শিল্পচর্চাও অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর শিল্পচর্চার একটা বিশেষ মনোযোগের দিক ছিল—কত রকমভাবে নানা ফর্মে, ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আঁকা যায়। ক্লান্তিহীন, নিরন্তর ছিল তাঁর এই প্রয়াস। এ রকম ষাটটি ছবি নিয়ে ১৯৮৬ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডনে একটা প্রদর্শনী হয়েছিল। দর্শকনন্দিত সে প্রদর্শনীর সব কটি ছবিই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।
১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ‘টারময়েল’ (বিক্ষোভ) সিরিজের বিশটি ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। এ সিরিজের ছবিগুলো সৃষ্টির পেছনের ইতিহাসটুকু খুবই অভিনব, চমত্কার। অসুস্থ পূর্ণেন্দু পত্রী এক অলস অপরাহ্নে বারান্দায় বসে ছিলেন। বারান্দায় ডিজাইন করা কালো মার্বেল পাথরের টাইলসগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করেই তাঁর চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে থাকে মানুষ—আন্দোলিত মানুষ। বিদ্রোহী মানুষগুলো কোনো অজানা লক্ষ্যের দিকে অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে। সেই গতিময়তায় ওই মানুষের দেহগুলো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, ভিন্ন এক অবয়ব পাচ্ছে অপরাজেয় এই মানুষগুলো। তখনই, অসুস্থ অবস্থাতেই পত্রী পাথরের টাইলস থেকে তাঁর নতুন ড্রয়িং সিরিজের কাজ শুরু করেন। কলকাতায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে ছোট-বড় বিশটি ছবি প্রদর্শিত হলেও এই সিরিজে তিনি আরও অনেক ছবি করেছিলেন। ঢাকায় কারও কারও কাছে এই সিরিজের ছবি রয়েছে।
পূর্ণেন্দু পত্রীর এত রকম বিভিন্নমুখী বিশাল সৃজনশীল কাজ ছাড়াও বিশেষ ‘হবি’র মধ্যে ছিল গণেশের মূর্তি সংগ্রহ। দেশ-বিদেশের ‘ছাইদানি’ জমানো। আর বই? সে এক বিশাল জগৎ, বিষয় হিসেবে যার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তাঁর সংগৃহীত ক্যাকটাসের সংখ্যা দেখে ধারণা করতে পারলাম, কত রকম অজানা-অচেনা ধরনের ক্যাকটাস হতে পারে। বাড়িজুড়ে পুরোনো মূর্তি, দেয়ালচিত্র আর মাটির লোকশিল্প।
পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে সেই পরিকল্পিত কথোপকথনের প্রথমেই জানতে পারি, ওই সময় তিনি প্রায় একই সঙ্গে চার-পাঁচটি বইয়ের প্রস্তুতিমূলক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মাল-মসলা সংগ্রহ করছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজটি ছিল উনিশ শতকের দিনপঞ্জি। তাঁর মতে, কাজটি শেষ করতে প্রায় দশ বছর লেগে যাবে। এ কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন কি না, তা আর জানতে পারিনি।
এ রকম একটা সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর কাজ তিনি কেন হাতে নিলেন? এর উত্তরে পূর্ণেন্দু পত্রী অত্যন্ত আবেগবিহ্বল হয়ে বলেন, ‘কোনো কোনো মহল, বিশেষ করে বামপন্থী বলে পরিচিত কিছু বুদ্ধিজীবী উনিশ শতকের মনীষী, মহৎ ব্যক্তিদের সমস্ত কাজকর্মকে অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁরা রাজা-মহারাজা বা জমিদার ছিলেন—সে কথা বলে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে নাকি সাধারণ মানুষের বা গণসংগ্রামের কোনো যোগাযোগ ছিল না।’ পত্রী বলেন, ‘এ ধরনের তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীদের “তত্ত্বকথা”র যথাযথ উত্তর দেওয়ার লক্ষ্য থেকেই উনিশ শতকের দিনপঞ্জি করতে শুরু করেছি। আমি কিছু ঘটনাবলি তুলে ধরব শুধু, মন্তব্য করব না। দিনপঞ্জি থেকেই বেরিয়ে আসবে উনিশ শতকের মনীষীদের ভূমিকা কী? প্রগতিপন্থী, না প্রতিক্রিয়াশীল?’
পূর্ণেন্দু পত্রী আরও বলেন, ‘উনিশ শতক দেখতে গিয়ে আমি অভিভূত হয়ে আছি। ধরা যাক, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কী করেছেন? তিনি ছয়-সাতটা ভাষা শিখেছেন। বই অনুবাদ করেছেন। স্ত্রী-শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে বহু কাজ করেছেন। আর বিদ্যাসাগর? তিনি তো সহজ বাংলা গদ্য ভাষা প্রচলনের চেষ্টা না করলেও পারতেন। আমরা কীভাবে বলব, আমরা উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে এগিয়ে আছি? আমরা তাঁদের চেয়ে বড়?
‘উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী সমাজ-সংস্কারকদের সবকিছু নিজেদের গড়তে হয়েছে। নিজেদের হাতে, নিজেদের গুণে-অর্থে করতে হয়েছে। আর এখন আমাদের সব দাবি সরকারের কাছে। সরকারের কাছ থেকেই নিই, বিদেশি সংস্থার কাছে হাত পাততেও বাধে না। আমরা নিজেরা কিছু করি না। শুধু তত্ত্ব দিই।’
তখন তিনি বলেছিলেন, ‘বিশাল বেদনা নিয়ে বাস করছি। নিজের কাজ ছাড়াও কিছু একাডেমিক কাজ করে যাচ্ছি। পরে যদি কারও কোনো কাজে লাগে।’ পত্রী বলেছিলেন, ‘কী করব বলুন, আমার বহু রকমের ব্যামো। উনিশ শতকের মানুষের মতোই বলতে পারেন। গ্রিক ট্র্যাজেডির লোক হলে তাকে কে বাঁচাবে বলুন?’
উনিশ শতকের দিনপঞ্জি প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বসাহিত্য প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রনাথের কলকাতা এবং রবীন্দ্রনাথ ও সিনেমা—এই বিষয়গুলোর ওপর কাজ করছিলেন। বই করবেন ভেবেছিলেন।
সেদিন পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে আলোচনাকালে যে প্রশ্ন বা বিষয়টা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেশি আলোচনা হয়েছিল, তা হলো শিল্প, সাহিত্য বা সংস্কৃতিজগতের কোনো কর্মীর একাধিক ক্ষেত্রে বা বহু কাজ করা কতটুকু যুক্তিসংগত?
পূর্ণেন্দু পত্রী গভীর আবেগে বলেছিলেন, ‘দেখুন, এ বিষয়ে বলতে গেলে নিজের কথা এসে যায়, আমাকে অহংকারী বলবেন হয়তো অনেকে। অনেকে বলেন, এত দিকে কাজ না করলে ভালো করতেন? কিন্তু কী করি বলুন, এত দিক নাড়াচাড়া করে বুঝলাম, কিছুই করতে পারলাম না। বাংলা ভাষায় লিখতে-পড়তে পারি। ইংরেজি ছাড়া অন্য কোনো বিদেশি ভাষা জানি না। ফরাসি বুঝি না, অনুবাদ থেকে বোদলেয়ার, আপোলিনের, এল্যুয়ার, আরাগঁকে জানতে-বুঝতে হয়, তখন বেদনা হয়।
‘আজকাল কেমন জানি জব ডিভিশন হয়ে গেছে। কবি কবিতা লিখবেন, গল্পকার-ঔপন্যাসিক শুধু গল্প-উপন্যাস লিখবেন, শিল্পী শুধু ছবি আঁকবেন। আর অন্য কোনো দিকে তাকাবেন না। তাঁর আর কোনো দায়িত্ব নেই। পৃথিবীর অন্য দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে এটা মেলে না। অথচ দেখুন রেনেসাঁর যুগে, লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর কথা ভাবুন তো। ইতালির লিয়োঁ বাতিস্তা আল ব্রেতি ও লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে ব্রিটিশ শিল্পবিশেষজ্ঞ কেনেথ ক্লার্ক “ইউনিভার্সেল ম্যান” বা “বিশ্বমানব” বলে আখ্যায়িত করেছেন।
‘দ্য ভিঞ্চির আটচল্লিশ বছর আগে আল ব্রেতির জন্ম। মূলত তিনি ছিলেন স্থপতি। কিন্তু তিনি ছবি আঁকতে জানতেন। ভাস্কর্য গড়তে পারতেন। তাঁর আগ্রহের বিষয়গুলো ছিল গান, অঙ্ক, ভাষা, আইন, অশ্বচালনা প্রভৃতি। তা ছাড়া তিনি আবিষ্কার করেছিলেন এমন উপায়, যা দিয়ে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা যায়। প্রস্তুত করেছিলেন ক্যামেরার অব্সকিউরা, বই লিখেছেন অসংখ্য। তবে স্থাপত্য বিষয়েই তাঁর মূল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল ব্রেতি যখন ঘুমোতে যেতেন, তখন শিয়রে জ্বলত মোমবাতি, সেটি নিভে না যাওয়া পর্যন্ত পড়তেন কবিতা অথবা ইতিহাস।
‘আর মহান শিল্পী দ্য ভিঞ্চি? বহু বছর তিনি ব্যয় করেছেন খাল কাটার ব্যাপার নিয়ে। এতেই তাঁর বহু সময় চলে গেছে। আমরা হয়তো ভাবব, সময়ের কী অপব্যয়!
‘মহাকবি গ্যেটের কথা ভাবুন। উদ্ভিদবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রঙের ওপর বহু কাজ করেছেন। রঙের ব্যাকরণ বলতে পারতেন। রঙের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। এসবই তো কবির কাজ।
‘ভাবুন, রুশি সের্গেই আইজেনস্টাইনের কথা। তিনি স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্র। বহুভাষাবিদ, ঘুরেছেন অনেক দেশ। নৃতত্ত্ব, ইতিহাসের ওপর পড়াশোনা করেছেন, রঙিন ছবির ওপর সে সময়ই বহু ভেবেছেন, আলোচনা করেছেন। বিশ্বসাহিত্য থেকে যখন-তখন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে চমকে যেতে হয়।
‘দেখুন, সব সময় কবিরাই তো পৃথিবীর অহংকারী শাসক। গিয়োম আপোলিনের পিকাসোকে পরিচিত করিয়েছেন। কিউবিজমের ব্যাখ্যাও তাঁরই দেওয়া। এমনকি সিনেমা যে একটা বড় আর্ট-ফর্ম হতে পারে, সেটাও তিনি বলেছিলেন। তিনি কবি, ছবি এঁকেছেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনও করেছেন। এভাবে দেখা যায়, সব কবিই শিল্প-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। কবির এই যে বিশাল সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, সব আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, এখন এমনটা কেন হবে না? এখন কবির শুধু কবিতা লিখেই শেষ? আর কোনো দায়দায়িত্ব নেই? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের মেলে না। একাধিক বিষয়ে চর্চা করাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়। এটাই হওয়া উচিত। আমি ব্যাপারটাকে এভাবেই দেখি।’
আমি জানতে চাই, রেনেসাঁর যুগ বা বিশ্বমানব প্রসঙ্গ এবং তাঁর উদাহরণগুলো সবই অতীতের। বর্তমান যুগেও কি এ রকম উদাহরণ দেওয়া যায়?
‘অবশ্যই, এ রকম এখনো আছে। ভাবুন, জার্মান ঔপন্যাসিক গুন্টার গ্রাসের কথা। গল্প-উপন্যাস লেখেন। ছবি আঁকেন। মূর্তি গড়েন। সিনেমায় কাজ করেন সহায়তাকারী হিসেবে। রাজনীতি-সচেতন লোক। যুদ্ধ বা তারকাযুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়।
‘ভাবুন, বিশ্বনন্দিত ফরাসি ফটোগ্রাফার হেনরি কার্তিয়ের ব্রেসোঁর কথা। রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। নাৎসিদের জেলে অত্যাচারিত হয়েছেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে কাজ করেছেন, ডকুমেন্টারি ছবি করেছেন। সুররিয়ালিস্ট কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এত সব অভিজ্ঞতার পর মানুষটি যখন একটা লক্ষ্য স্থির করে নেন, তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য অনেকের চেয়ে বড় হতে বাধ্য। তাই সবটাই একটা সামগ্রিক ব্যাপার।
‘শেক্সপিয়ার, দান্তে, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ, আইজেনস্টাইন পড়লে মনে হয় আমাদের কত বড় হওয়া উচিত। এখনো আমাদের সামনে কত সব সমস্যা রয়ে গেছে। তাহলে ভাবব না কেন? যখন বইয়ের পাতা উল্টাই, তখন দেখি পূর্বসূরিরা কত কাজ করে গেছেন। তখন কষ্ট পাই।’
জিজ্ঞেস করি, কেনেথ ক্লার্ক আল ব্রেতি ও দ্য ভিঞ্চিকে ‘বিশ্বমানব’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নিশ্চয় ‘বিশ্বমানব’ পর্যায়ে পড়েন?
পত্রী বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিশ্চয়ই বিশ্বমানবের পর্যায়ে পড়েন। তবে এখন বিদেশে তেমন আলোচনা হয় না। আসলে ২০০ বছরের আগে কোনো মানুষের “গ্রেটনেসের” বিচার হয় না। শেক্সপিয়ার বা দান্তেরও হয়নি।’
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর বহুমুখী কাজে নিমগ্নতা ছিল। এখনো তিনি তা করে চলেছেন, কেন?
পত্রী বলেন, ‘দেখুন, এখনো প্রতিদিন মনে হয়, গতকালের চেয়ে আজ রবীন্দ্রনাথকে বেশি জানলাম। এমন কোনো দিন যায় না, যেদিন তাঁর লেখা বা তাঁকে নিয়ে লেখা পড়ি না। তখনই মনে হয়, তাঁর সম্পর্কে আরও কিছু জানলাম। আমার কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিনই আবিষ্কারের বিষয়।
‘রবীন্দ্রনাথ কী রকম আধুনিক মানুষ ছিলেন? রামকিঙ্কর গড়লেন দুটি রবীন্দ্রনাথ। একটি ঝুঁকে পড়া রবীন্দ্রনাথ, আরেকটির দুই চোখ দুই জায়গায়। আধুনিক রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয় পেয়েই না রামকিঙ্কর এমন কাজ করতে পেরেছেন। আবার কবে এমন মানুষ হবে, জানি না। ইউরোপীয় শিল্পকলার ওপর বক্তৃতা হবে, বক্তারা বিদেশ থেকে এসেছেন, রবীন্দ্রনাথ গিয়ে প্রথম সারিতে বসেছেন। উনি না এলে যদি নন্দলাল প্রমুখেরা না আসেন।’ পূর্ণেন্দুদা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখেছেন অনেক, এঁকেছেনও অনেক। তাঁর আঁকা একটি রবীন্দ্রনাথ চেয়ে নিয়েছিলাম।
সচেতন জীবনের সূচনা থেকে, পঞ্চাশের দশকের শুরুতে প্রায় ছয়-সাত বছর পূর্ণেন্দু পত্রী বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তেভাগা আন্দোলনের জায়গায় গিয়ে থেকেছেন, কৃষক কর্মীদের সঙ্গে মিশেছেন। সে সময়টায় তাঁর রাজনীতিময় জীবন ছিল। লেখার প্রথম উত্সাহও এসেছিল রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে। পোস্টার আর প্রচারধর্মী প্রচুর কাজ করেছেন।
এ প্রসঙ্গে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেন, ‘১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরির ঘটনাবলিতে আঘাত পেলাম। সেখানে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান, সেটা দমন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক হস্তক্ষেপ—সমগ্র ব্যাপারটা মেনে নিতে পারিনি; ঘা খেলাম। রাজনীতি থেকে, লেখা থেকে দূরে সরে গেলাম। প্রচ্ছদ আঁকা, কমার্শিয়াল কাজ আর সিনেমার দিকে ঝুঁকে গেলাম। পরে কখনো রাজনীতির সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর তৈরি হয়নি।’
পূর্ণেন্দু পত্রী বলেন, ‘এসব কিছুর প্রায় দুই দশক পরে, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে পুনরায় ফিরে যাই সেই পূর্বের চিন্তায়। দেখতে পাই, বুঝতে পারি, অন্যায়-অবিচার আর শোষণ কাকে বলে? আমি নিজেকে একজন রাজনৈতিক সচেতন মানুষ বলে মনে করি। আমি প্রগতির পক্ষে। সে লক্ষ্যে থেকে যা কিছু করা সম্ভব সেটা করি; সচেতনভাবে করি—কারও নির্দেশ বা পরামর্শে নয়।’
যখন এই কথাগুলো বলেছিলাম পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গে, বয়স তখন তাঁর প্রায় চুয়ান্ন বছর। তাঁর মৃত্যু হলো চৌষট্টি বছর বয়সে। কলকাতার কাছে হাওড়া জেলায় নাকোলী গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। চাচা নিকুঞ্জ পত্রীর সুন্দর রুচির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পূর্ণেন্দু মাটির পুতুল গড়ার প্রথম শিক্ষা পেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে। ছবি আঁকা ও শিল্পচর্চার পেছনের উত্সাহও ছিল তাঁরই।
শেষ বছরগুলোতে তেমন সুস্থ ছিলেন না পূর্ণেন্দু পত্রী। হাঁপানির সমস্যা ছিল তাঁর। ছিল ঘাড়ে-পিঠে ব্যথা। সেই সঙ্গে মদ্যপান আর ধূমপান তাঁকে কতটা সাহায্য করেছিল সেটা বলা কঠিন। বিছানায় বসে বইয়ের ওপর কাগজ বা খাতা রেখে লিখতেন, কিছুক্ষণ সোফায় শুয়ে বিশ্রাম নিতেন, তখন তাঁর কাছে লেখার চেয়ে আনন্দের আর কিছু ছিল না, লেখাই ছিল জীবন।
শিল্প-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় অক্লান্ত পূর্ণেন্দু পত্রীর বিরামহীন সৃষ্টিশীল কর্মের নান্দনিক বৈভব তাঁর প্রত্যেক পাঠক ও দর্শক-শ্রোতাকে নিয়ে যায় সুন্দর আর আনন্দের জগতে, যাঁর সবকিছুই মানুষের জন্য উত্সর্গীকৃত, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য নিবেদিত। বর্তমানে আমাদের সময়ে চারদিকে যখন হতাশা আর ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী, তখন পূর্ণেন্দু পত্রী লেখা, আঁকা, ছবি আর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমাদের জন্য যতটুকু যা করেছেন, এর জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।
১৯৮৭ সালের ১৭ জুলাই কলকাতায় রূপসী বাংলার দুই কবি বইটি আমাকে উপহার দিতে গিয়ে লিখে দিয়েছিলেন, ‘রূপসী বাংলার অর্ধেকটা তো ওপারে, যা আমার দেখাই হলো না এখনো। যেটুকু দেখা, সে শুধু অন্যের মুখে মুখে শুনে। অধীর হয়ে অপেক্ষা করে আছি। বাংলাদেশ দেখা হলে তবেই জানব আমি গোটা বাংলার মানুষ।’ শেষমেশ ১৯৮৯ সালে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। না এলেও তাঁকে আমরা জানতাম গোটা বাংলার মানুষ বলেই।
আরও পড়ুন
- তাঁদের কথা মনে রাখব
- জর্জ হ্যারিসন ও দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ
- স্টোরি অব এ রিয়েল ম্যান
- পূর্ণেন্দু পত্রী: গোটা বাংলার মানুষ বলেই